আজকে আমরা আলোচনা করবো উত্তরী পদ্ধতির গীতি প্রকার

Table of Contents
উত্তরী পদ্ধতির গীতি প্রকার
কণ্ঠসঙ্গীতে নানা প্রকারের গান আছে । প্রত্যেক প্রকারের গীতশৈলী— মানে গাইবার ভঙ্গি (Style) আলাদা-আলাদা । এখানে পাঠ্যান্তর্গত কয়েক প্রকার গানের পরিচয় দেওয়া হচ্চে সংক্ষিপ্ত ভাবে।
স্বরমালিকা (বা সুরাবর্ত )
কেবলমাত্র স্বর দিয়ে রচিত হয় বলেই এই গীতি প্রকারের নাম রাখা হয়েছে স্বরমালিকা। স্বর ছাড়া অন্য কোন কথা এতে থাকে না । যে-কোন রাগে এই গান রচিত হতে পারে। স্বরগুলিকে সুন্দরভাবে রচনা করে, তালে বেধে গাইতে হয়।
ধ্রুপদ
খ্যাল গান প্রচলিত হবার আগে ধ্রুপদ গানের বহুল প্রচলন ছিল। এই শৈলীর গানগুলি ভাব, ভাষা, রাগের শুদ্ধতা, ছন্দের বৈচিত্র্য, গীতরীতির গাম্ভীর্ষ’ প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ । এর অবয়ব বা তুক হ’ল প্রধানত চারটি— স্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। চোতাল, সুরফাঁক (সুরফাকতালকে শালতাল ও বলা হয় ), তেওরা প্রভৃতি তালে নানা লয়কারী সহ পাথোয়াজের সঙ্গে গাওয়া হয়। আজকাল অবশ্য তবলাও বাজে । তাতে কিন্তু এর বৈশিষ্ট ক্ষম হয়। পেদ গাইবার আগে নোম-তোম ইত্যাদি বাণী দ্বারা আলাপচারী করা হয়। মীড়, কণ, গমক প্রভৃতি এতে বেশি প্রযন্তে হয়। তানের ব্যবহার এতে হয় না । খ্যাল গানের ব্যাপক প্রচারের ফলে প্রপদ প্রচলন বর্তমানে কমে গেছে।
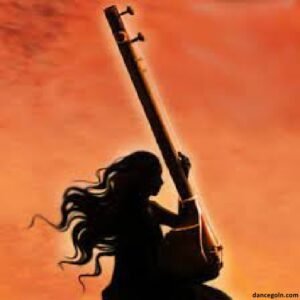
ধমার বা হোরী
ধামার একটি তালের নাম । কলাবত্তরা মানে ধ্রুপদ গায়কেরা, বসন্ত ঋতুতে বিশেষ ক’রে হোলীর সময় ধমার তালে যে হোলী বা হোরী গাইতেন, সেই গীতশৈলীটিই পরে ধমার বা হোরী নামে চিহ্নিত হয়ে গেল । নিরানব্বইটি ধমার গানের রচনায় রাধাকৃষ্ণের হোলিলীলার বর্ণনা আছে। তাই এই গান শ,ষ, হোরী নামেও চিহ্নিত হ’ত । শতকরা ধামার গানের রচনা পদ অপেক্ষা লঘ; প্রকৃতির। আজকাল যেমন খালের পর ঠুমরী গাওয়া হয়, প্রপদী যগে তেমনি গ্রুপদের পর ধমার গাইবার রেওয়াজ ছিল । এতেও নানা লয়কারী থাকে। ধ্রুপদের সঙ্গে সঙ্গে ধমার গানেরও প্রচলন কমে যাচ্চে ।
খ্যাল
ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মামদ সুলতান যে-সময় পাঞ্জাবে বসবাস আরম্ভ করেন, সেই সময় তাঁর সঙ্গে একদল ইয়ামিনী গায়ক ছিলেন। তাঁদের বলা হ’ত কওয়াল। তাঁদের গীত-রীতির কিছুটা সংস্কার ক’রে অমীর আরো প্রবন্ধ অঙ্গের নকশ-এ-গলে কলবোনার সৃষ্টি করেন। এগুলি ছিল আরবী ও ফারসী ভাষার সংমিশ্রণে রচিত ভারতীয় ঢঙের গান । তারপর চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে অমীর সূরো গীতরীতির বৈশিষ্ট- গালি মিশিয়ে সৃষ্টি করলেন ছোট খাল। বিলম্বিত লয়ের বড় খ্যালের জন্ম হয় পঞ্চদশ শতকে। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ্, শাকীকে এই পদ্ধতির খ্যাল গানের আবিষ্কর্তা বলা হয় ।
রাগের নিয়মগুলি পালন করে নিজ কল্পনার সাহায্যে নানা রকম স্বরবিস্তার, তান, বোলতান, সরগম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ক’রে রিভাল, তিলওয়াড়া, একতাল প্রভৃতি ভালে নিবদ্ধ করে খ্যাল গাওয়া হয়। লয়ের বিভিন্নতা হিসেবে এর দুটি প্রকারের একটি হ’ল বিলম্বিত বা বড় খাল, অপরটি মধ্য বা দ্রুত লয়ের ছোট খাল । এর অবয়ব স্থায়ী বা অন্তরায় সীমিত। অধিকাংশই শৃঙ্গার রসাত্মক হয়ে থাকে।

টপ্পা
অনেকের ধারণা, প্রাচীন বেসরা গীতি থেকেই টপ্পার জন্ম। ভিন্ন মতে বলা হয়, যে-সময় মধ্য এশিয়ার কওয়ালরা এসে পঞ্জাবে বসবাস আরম্ভ করেন, সেই সময় তাঁরা তাঁদের দেশীয় গানের সঙ্গে এদেশীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য মিশিয়ে যে বিচিত্র শৈলীর গান গাইতেন, সেই গানই হ’ল টপ্পা ।
টপ্পা এক সময় সভ্য সমাজের বহির্ভূত ছিল। পরে লখনৌ-এর প্রসিদ্ধ গায়ক গুলাম নবীশোরী এর সংস্কার করে ভদ্র সমাজে প্রচার করেন। এই গান শৃঙ্গাররসাত্মক চটুল প্রকৃতির গান। কথা এতে কম। পাঞ্জাবী ভাষাতেই রচিত। বিশেষ ধরণের দানাদার তান দিয়ে গানের কথাকে বিন্যাস করা হয়। এরও অবয়ব দলটি, স্থায়ী ও অন্তরা। প্রধানত কাফী, খমাজ, পলি,, ঝি ট, বারোয়াঁ ভৈরবী প্রভৃতি রাগে টপ্পা গাওয়া হয়। টপার ঠেকাও একটু ভিন্ন ধরণের হয়। টপ পাও আজকাল প্রায় শোনা যায় না ।
ঠুমরী
খাল ও টপ পার মত ঠুমরীর প্রকারটিও এক সময় গণী সমাজে অপাংক্তেয় ছিল। এই গানের প্রচলন ছিল বাঈজীদের মধ্যে। লোকরঞ্জনের জন্য নানা রাগের সংমিশ্রণ ক’রে বাঈজীদের নানা অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাব (ভাও ) প্রকাশ করে নৃত্য সহযোগে গান পরিবেশিত হ’ত। শঙ্গাররসই এর প্রধান উপযোগী। জনরুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল বিশিষ্ট খ্যায়ালিয়ারা ও খালের পর ঠুমরী পরিবেশন ক’রে থাকেন সঙ্গীত সম্মেলনে ।
ঠুমরী বা ঠুংরী ভাবপ্রধান গান। রাগের বিশুদ্ধতা অপেক্ষা ভাব- অভিব্যক্তির দিকেই লক্ষ্য রাখা হয় বেশী। তাই জনসাধারণের মধ্যে এর প্রচার বেড়ে গেচে ।
এর জন্মবৃত্তান্ত সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে অনেকেই মনে করেন, লখনৌ এর সাদিক অলি খাঁ নাকি এর জন্মদাতা। অতঃপর কদরপিয়া ললনপিয়া প্রভৃতি অনেকে ঠুমরী রচনা করেন।
ভৈরবী, পীল,, কাফী, খমাজ, তিলং, তিলককামোদ প্রভৃতি রাগে শান্তভাবে পদবিন্যাস ক’রে ঠুমরী গাওয়া হয়। এতে প্রধানতঃ যৎ, দীপচন্দী, ধমালী, পাঞ্জাবী, অন্ধা, ত্রিতাল প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়। ছোট-ছোট তান, রেকী, গিটকিরী ইত্যাদি দিয়ে তাকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়।
দুই অঙ্গে ঠুমরী গাওয়া হয়—পূর্বী ও পাঞ্জাবী অঙ্গে। বেনারস ও লখনৌ ঘরানার ঠুমরী পূর্বে অঙ্গের পর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানত পূৰ্বী অঙ্গেই প্রযুক্ত হয়। পাঞ্জাবী ঠুমরীতে টপ পার দানাদার তানের প্রাধান্য বেশি। তালের মাত্রায় মাত্রায় কথা সংযোগ ক’রে নাচের ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক প্রকার ঠুমরী গাওয়া হয়, যাকে ঘনাক্ষরী ঠুমরী বলা হয় । ঠুমরীর আরেকটি প্রকারের নাম ‘দাদরা’।

তরানা
তরানার গায়নভঙ্গি খ্যালের মত হোলেও, খ্যালে যেমন গীতি কবিতা থাকে, তরানা তেমনি রচিত তদরে দানি, তদিয়ানা, তনদেরে ওদানি, তনোম,, ইয়ললী, ইয়লম ইত্যাদি কতগুলি অর্থহীন ভাষা দিয়ে। অর্থহীন ভাষা বলাটা সমীচীন কিনা জানিনা । কারণ আজকাল কোন-কোন গণী উত্ত শব্দগালির অর্থভেদের প্রয়াস চালাচ্চেন । মাঝে মাঝে তবলা বা পাখোয়াজের বোলও রচনার মধ্যে থাকে। ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল প্রভৃতি তালেই সাধারণত এগুলি গাইতে শোনা যায় । তবলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানা লয়কারী এতে দেখান হয়। রাগ আর তালই এর প্রধান উপজীব্য । খ্যাল গাইবার পর তরানা গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন শিল্পী। কথক নাত্যের সঙ্গেও তরানা গাওয়া হয়।
গজল
গজল শব্দটি পারসিক ভাষার। এই স্টাইলটিও নাকি ঐ দেশেরই। যতদূর জানা যায়, অমীর খসরোই এ-গানকে এ-দেশে প্রচার করেন উদং ভাষায় । তাঁর হস্তক্ষেপের আগে গজল ছিল নিম্নরা চির প্রেম সঙ্গীত। কথা এতে বেশী, সুরের প্রাধান্য নেই । গীতি কবিতার ভাব প্রকাশই গজলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি স্থায়ী এবং অনেকগুলি অন্তরা এতে থাকে, যা প্রায় একই সুরে গাওয়া হয় এবং আজকাল অবশ্য উন্নতমানে কাব্যরসাশ্রিত গজল শোনা যায়।
সম্রাট জাহাঙ্গীর, নরেজহান, নবাব ওয়াজিদতালি শাহ, প্রভৃতির রচনার সন্ধানও পাওয়া গেছে। মীর্জা গালিব, জওক, আরজ, প্রভৃকি অনেক কবি ভালো ভালো গজল রচনা করে গেছেন । কাজী নজরুল ইসলাম উদ গজলের অনকরণে অনেক বাংলা গজল রচনা করেচেন ।
এই ভাবপ্রধান গানগুলি প্রধানত টপ পার ও ঠুমরীর জন্য নির্দিষ্ট রাগ ও দীপচন্দী, পণ্ডো ইত্যাদি তালে গাওয়া হয়।

ভজন
এক কথায় ভক্তিরসাশ্রিত গানই হ’ল ভজন। অর্থাৎ যে-গানগুলি তুলসীদাস, কবীর দাস, সুরদাস, মীরাবাঈ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ভক্ত সাধক-সাধিকারা রচনা ক’রে গেছেন, সেইগুলিকেই ভজন বলা হয় ।
রচনার ভাব অনুসারে ভজন গানে সুরারোপিত হয়। রাগের বিশুদ্ধতা এখানে গৌণ ভক্তিভাবই প্রধান হওয়ায় সুরের বা তাল ও লয়ের কোন মারপ্যাঁচ এতে থাকে না। আত্মনিবেদনই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। গায়নশৈলীর মধ্যেও গায়ককে সেই দিকেই বেশি লক্ষ্য রাখতে হয়।
হোলী
ধ্রুপদী যুগে অভিজাত কলাকারেরা যে হোরী গাইতেন, তা যে ধমার নামে প্রচলিত হয়েছে, সে-কথা আগেই বলেছি। কিন্তু গ্রামের মানরে যখন তাঁদের হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেন গানের মাধ্যমে, তখন তা লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বামীনরা এঁদের বিভিন্ন উৎসব- অনষ্ঠানে, প্রাকৃতিক পরিবেশে, বিভিন্ন ঋতুতে মনের আনন্দে যে-সব গান গাইতেন, স্থান-বিশেষে সেইগালিই নানা নামে অভিহিত হয়েছে। হোলী, কজরী, চৈতী, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, সারি জারী, মালসী, গম্ভীরা, ভাদা প্রভৃতি সবই এই লোক-সঙ্গীতের অন্তর্গতি।
হোলী নামেই বোঝা যাচ্ছে, এটি দোল উৎসবের গান। শৃঙ্গার রসাত্মক এই গানে রাধাকৃষ্ণের দোললীলার বর্ণনা থাকে। হোলীর সময় গ্রামীন মেয়ে পরেেেষরা সমবেত ভাবেও হোলী গান গেয়ে থাকেন ।

চৈতী
চৈত্র মাসে এই শৈলীর লোকগীত গাওয়া হয় প্রধানত বিহার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিহারের প্রধানতম লোকসংগীত হল চৈতী। শঙ্গার রসের যে দুটি পর্যায়ে আছে—সংযোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ মিলন ও বিরহ। চৈতী বিরহ পর্যায়ে পড়ে। এতে রাম-সীতার বর্ণনাই থাকে বেশী ।
কজরী বা কঙ্গনী
চৈতী যেমন বিহারের চৈত্র মাসের গান কজলী বা কারী তেমনি উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত ব্যসিঙ্গীত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথির দিন রাজ্যে ( প্রধানত মিজাপরে, বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চলে) গ্রামীন মেয়েরা “কজলী ব্রত উদযাপন করেন। নতুন শাড়ী পড়ে, অলংকারে সুসজ্জিতা হবে, হাতে-পায়ে মেহেদী রঙের ছোপ লাগিয়ে এরা কজলী দেবীর পুজো করেন এবং ভাইদের হাতে বেধে দেন ‘জরঈ’ ( রাখীর মত )। সারা রাত জেগে তাঁরা শৃঙ্গার-প্রধান কজলী গান গেয়ে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেন । বারাণসী ও মির্জাপুরেই হ’ল এই গীতশৈলীর প্রধান কেন্দ্র। কাশীতে “ললোরক ছট” নামে আরেকটি পরব হয়। এই পরব উপলক্ষ্যেও কজরী গীত হয়। সমারোহের সঙ্গে। হিন্দু-মাসলমান নির্বিশেষে সব শিল্পীরাই সমবেত হ’য়ে এই উৎসবে আনন্দ করেন ।
বিরহ ও মিলনের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা কজরীতে থাকে। ভক্তি রসাত্মক কিছ, কজরী গানও আছে। সাধারণত দলের ‘মুখিয়ারা’ই (মোড়ল ) স্থানীয় ভাষায় নতুন নতুন কছরী রচনা করেন এবং দলের সবাইকে শিখিয়ে দেন।
আরও দেখুনঃ
